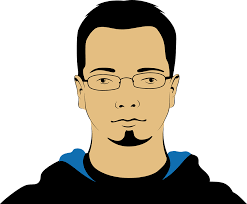অজয় দাশগুপ্তঃমোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) ১৯২০ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। এ বছরেই জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে অসহযোগ কর্মসূচির সফল প্রয়োগ করেছিলেন ১৯৭১ সালে। কাকতালীয় হতে পারে আরও একটি তথ্য- মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সর্বাত্মক অসহযোগিতার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন ৫১ বছর বয়সে। ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই অনন্য ঘোষণাও দিয়েছিলেন ৫১ বছর বয়সেই। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণের প্রথম ধাপে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি, যা ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ।
বঙ্গবন্ধু ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘সত্যিই ভদ্রলোক জাদু জানতেন।’ [পৃষ্ঠা-৮১]
বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গেও নির্দ্বিধায় বলা চলে, তিনি কেবল ‘পোয়েট অব পলিটিক্স’ নন- বাঙালিরা তার কথা শুনত মুগ্ধ হয়ে, যেন জাদুর সোনার কাঠির স্পর্শ মিলেছে। তিনি সাত কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন। সংকল্পবদ্ধ করেছেন। তারা শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সর্বাত্মক সফল করেছিল। আবার যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সম্মুখ রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এলো, তখনও বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। ‘তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক’- এমনটিই বাস্তবে ঘটেছিল। আর এটাই মহাত্মা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা-কৌশলে মৌলিক পার্থক্য টেনে দেয়। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে প্রকৃত অর্থেই আসমুদ্রহিমাচলের কোটি কোটি নারী-পুরুষ-শিশু শামিল হয়ে যায়। কেঁপে ওঠে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত। কিন্তু ১৯২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের চৌরিচেরায় পুলিশ-জনতার সংঘর্ষের জেরে মহাত্মা গান্ধী ১২ ফেব্রুয়ারি এ আন্দোলন আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করে নেন। ব্রিটিশ শাসকদের নির্দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুলি করে হত্যার প্রত্যাঘাতে ক্ষুব্ধ জনতার থানায় হামলা চালানোর ঘটনা তিনি মেনে নিতে পারেননি। যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখতে হবে- এটাই ছিল তার সংকল্প। একই কারণে নেতাজী সুভাষ বসু ও মাস্টারদা সূর্যসেনের সশস্ত্র সংগ্রামের কৌশলও তার অনুমোদন পায়নি। অন্যদিকে, বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ‘সংলাপ’-এ বসতে যেমন দ্বিধা করেননি, তেমনি ২৫ মার্চ গণহত্যা শুরুর খবর নিশ্চিত হয়েই পূর্ব নির্ধারিত বার্তা প্রেরণ করেন সর্বত্র-‘দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান।… পবিত্র মাতৃভ‚মি থেকে শেষ শক্রকে বিতাড়িত করুন।’ শান্তিপূর্ণ অসহযোগ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম, যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি।
মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটাতে প্যাসিভ রেজিট্যান্স বা ‘অক্রিয় প্রতিরোধের পথ’ বেছে নিয়েছিলেন। নিষ্ঠুর শাসকদের বিরোধিতায় তিনি সক্রিয় পন্থা অনুসরণ করেননি। বরং শাসকদের নির্দেশ, আইন ইত্যাদি অমান্য করার পথ গ্রহণ করেন। বাস্তবে এ কৌশল খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়। জনগণ আরও বেশি বেশি করে আন্দোলনে শামিল হয়ে যায়। তিনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ধাপে ধাপে সংগঠিত করার লক্ষ্যে বহু ধরনের কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। জনগণের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হয়। সে-সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশও আমরা স্মরণ করতে পারি। ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ ব্রিটিশ সরকার বিচারপতি সিডনি রাওলাটের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে চরম নিপীড়নমূলক আইন জারি করে। রাওলাট অ্যাক্ট নামে পরিচিত এ আইন বলে ভারতবর্ষের যে কোনো লোককে গ্রেফতার ও যত দিন খুশি আটক রাখা, গোপন বিচার অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র ও বাগ্-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি ক্ষমতা শাসকদের প্রদান করা হয়। মহাত্মা গান্ধী এ আইনের প্রতিবাদে ভারতবর্ষ জুড়ে হরতাল আহ্বান করেন ৩০ মার্চ। পরে নতুন তারিখ নির্ধারিত হয় ৬ এপ্রিল। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিওয়ানাবাগে শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ-মিলিটারি গুলি চালিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রাজপথের সংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং পদযাত্রার প্রস্তাবও করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ভারতবাসী কতটা সংকল্পবদ্ধ, এ ঘটনায় তার প্রমাণ মেলে। রাওলাট অ্যাক্ট জারি ও জালিয়ানাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদের মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালের ১ আগস্ট থেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার আহ্বান জানান। একই সময়ে ভারতবর্ষের মুসলিম নেতৃত্বের আহ্বান খিলাফত আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। তুরস্কে খিলাফত পুনর্বহালের দাবিতে পরিচালিত এ আন্দোলনের প্রতি মহাত্মা গান্ধী সমর্থন জানান। বিনিময়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সমর্থন মেলে। আন্দোলনের প্রভাবে একে একে ব্রিটিশ সরকারি অফিস ও কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ভারতীয়দের সরকারি স্কুল ও সরকারি চাকরি ত্যাগে উৎসাহিত করা হয় এবং তাতে বিপুল সাড়া মেলে। অনেকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন। আইনজীবীরা আদালত বর্জন করেন। বিদেশি পণ্য ও অন্যান্য সামগ্রী বর্জন করা হয়। চালু হয় স্বদেশি খাদি কাপড়। মাত্র এক বছরে বিদেশি কাপড় আমদানি ১০২ কোটি টাকা থেকে ৫৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। শাসকদের দেওয়া ‘রায় বাহাদুর-খান বাহাদুর’ এবং আরও অনেক ধরনের খেতাব বর্জনের আহ্বানও সফল হয়।
মহাত্মা গান্ধী সে-সময়ে ছিলেন কংগ্রেস দলের সভাপতি। দলকে সংগঠিত করার কাজেও তিনি মনোযোগ দেন। কংগ্রেসের সদস্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দল সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে। অনেক স্থানে খাজনা-ট্যাক্স প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ আন্দোলনে নারী সমাজ বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করে। তরুণ-যুবারাও দলে দলে শামিল হয়।
আন্দোলনের তীব্রতা ছিল অভাবনীয়। এর আগে আর কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতবাসীকে এক সূত্রে গাঁথতে পারেনি। শহর-বন্দর-গ্রাম, সর্বত্র মানুষের জাগরণ স্বাধীনতার জন্য। ব্রিটিশ শাসনের মেরুদন্ড ভেঙে পড়ছিল। চৌরিচেরার সহিংস ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন। এরপরও তাকে গ্রেফতার করে দুই বছর কারাদন্ড প্রদান করা হয়। কংগ্রেস দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীও কারাগারে। তরুণ-সমাজ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতি আস্থা রাখতে পারছিল না। কিন্তু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কৌশলের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর আস্থায় বিন্দুমাত্র চির ধরেনি। তিনি নতুন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ১৯৩০ সালে সামনে আসে নতুন ইস্যু- লবণ-কর। ভারতীয়রা লবণ উৎপাদন ও বিপণন করলে বাড়তি শুল্ক দিতে হবে, ব্রিটিশ শাসকদের এ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন তিনি। কংগ্রেস শুরু করে লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধী গুজরাট রাজ্যের সবরমতি আশ্রম থেকে সমুদ্র উপকূলে পায়ে হেঁটে রওনা হলে দলে দলে নারী-পুরুষ তাতে সাড়া দেন। গোটা দেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। লবণ সত্যাগ্রহ বা ডান্ডি মার্চ শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালের ৩০ মার্চ। এটা ছিল ব্রিটিশ সরকারের লবণ আইনের সরাসরি লঙ্ঘন। ২৪ দিনের এ মার্চ শুরু হয় ৭৮ জন বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে নিয়ে। ৩৮৪ কিলোমিটারের এ যাত্রা যতই ডান্ডির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, অংশগ্রহণকারী বাড়তে থাকে। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৬টায় মহাত্মা গান্ধী যখন লবণ আইন ভাঙেন, গোটা দেশ ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় লবণ আইনের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। আন্দোলনে শামিল হয়ে যায় কোটি কোটি ভারতবাসী। আইন লঙ্ঘন করে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে চলেন সমুদ্র উপক‚ল ধরে। তাকে ৪ মে মধ্যরাতে গ্রেফতার করা হয়। বিশ্বব্যাপী তার গ্রেফতারের খবরের পাশাপাশি লবণ সত্যাগ্রহ ও ব্রিটিশ সরকারের লবণ আইন নিয়ে খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এ আন্দোলনে ৬০ হাজারের বেশি ভারতীয় গ্রেফতার বরণ করেছিলেন।
মহাত্মা গান্ধীর পরবর্তী সাড়া জাগানো আন্দোলন ছিল ভারত ছাড় বা কুইট ইন্ডিয়া। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পাশে দাঁড়ানোর পূর্বশর্ত হিসেবে দাবি করলেন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের মুম্বাই অধিবেশনে ‘ডু অর ডাই’ স্লোগান তোলেন। ব্রিটিশ সরকার দ্রুতই দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। কংগ্রেসের গোটা নেতৃত্বকে জেলে পাঠানো হয় এবং তাদের বেশিরভাগ আটক থাকেন ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ব্রিটিশ সরকারের এ নিষ্ঠুর পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন দিয়েছিল কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে নিয়ে গঠিত ভাইসরয় কাউন্সিল, মহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সমর্থক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অনেক সদস্য। একদল ভারতীয় ব্যবসায়ীও ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে দাঁড়ায়। কারণ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তাদের ধনসম্পদ রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠছিল।
ব্রিটিশ শাসকরা দমননীতি চালিয়ে ‘কুইট ইন্ডিয়া’ বা ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করতে পারে। কিন্তু উপনিবেশিক শাসকরা বুঝতে পারে- ভারতবর্ষকে দামিয়ে রাখা যাবে না।
জনসম্পৃক্ততা: মহাত্মা গান্ধী প্রতিটি আন্দোলনেই সচেষ্ট ছিলেন যত বেশি সম্ভব মানুষকে অংশগ্রহণ করাতে। নারী-পুরুষ-শিশু, অচ্ছুৎ হিসেবে অবহেলিত জনগোষ্ঠী, ছাত্রছাত্রী-তরুণ-যুবক- সকলকে তিনি আন্দোলনে শামিল করতে পেরেছেন। স্বাধীনতার জন্য প্রকৃত অর্থেই তিনি সৃষ্টি করতে পারেন গণজাগরণ। রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি অসহযোগ ও শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনে তার লক্ষ্য ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- স্বাধীন দেশের জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি। বিদেশি পণ্য বর্জনের পাশাপাশি তিনি স্বদেশি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দেন। ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের সমান্তরালভাবে গড়ে উঠতে থাকে স্বদেশি বিদ্যালয়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দুটি পর্যায় সম্পর্কে জেনেছেন মূলত ইতিহাস পাঠ থেকে। কিন্তু ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন ঘটেছে তার চোখের সামনে। কোটি কোটি নারী-পুরুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনে শামিল করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তখন তিনি কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছেন। ছাত্রলীগের কর্মকান্ডে জড়িত। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতাকে আদর্শ মানেন। সে-সময়ের ইসলামিয়া কলেজকেন্দ্রিক মুসলিম ছাত্র-আন্দোলনে তিনিই ছিলেন পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুখ। রাজনীতির অঙ্গনেও সক্রিয়। ২৫-২৬ বছর বয়স হতে না হতেই অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ কমিটিতে সম্পাদকের পদের জন্য তার নাম বিবেচিত হয়।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে অনেকটা অপরিচিত পরিবেশের শহর ঢাকায় এসে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগে। নতুন পরিবেশে ছাত্রদের মধ্যে নিজের শক্ত অবস্থান করে নিতে তার সময় লাগেনি। ঢাকায় আসার কয়েক দিন যেতে না যেতেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন, যে সংগঠনটি মাত্র দুই মাসের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ও হরতাল (১১ মার্চ ১৯৪৮) সফল করে তোলায় ছিল সামনের সারিতে। হরতালে পিকেটিং করার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এক বছর পর তিনি ফের কারাগারে। এবারে অভিযোগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। কেবল কারাগারে প্রেরণ নয়, তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। এ সম্মান ফিরে পেতে তাকে অপেক্ষা করতে হয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয় পর্যন্ত। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ছাত্রত্ব কেড়ে নিয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও তাদের নির্বাচিত ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এ সংগ্রামে পালন করে অনন্যসাধারণ ভূমিকা। বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং এ পতাকা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মদান করে এ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারী-কর্মকর্তা। এও যে অনন্য মর্যাদা।
বঙ্গবন্ধু মাত্র ২৯ বছর বয়সে আওয়ামী মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি বা যুগ্ম সম্পাদক। তখন তিনি কারাগারে। মুক্তি পেতে না পেতেই নতুন মিশন- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানের সমমনা গণতান্ত্রিক শক্তিকেও তাতে শামিল করে পাকিস্তানভিত্তিক একক রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। এ মিশন নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নির্দেশে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তান। তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার পর তার স্থান হয় কারাগারে- একটানা প্রায় আড়াই বছর। এ-সময়ের মধ্যেই ২১ ফেব্রুয়ারির অমর গাঁথা রচিত হয়ে গেছে। কারাগারে কিংবা মাঝেমধ্যে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে থাকার সুযোগে তিনি নিজেকে কেবল আন্দোলনেই সম্পৃক্ত রাখেননি, যথাযথ দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হলে তিনি জেলে থেকেই তাতে একাত্মতা ঘোষণার জন্য অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাতে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিচ্ছে- এমনটিই তিনি চেয়েছিলেন। ‘জনসমর্থন ছাড়া বিপ্লব হয় না- আমার দেখা নয়াচীন (পৃষ্ঠা ২৪) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগেরই ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে চায়নি। দিনের পর দিন রাজপথের সংগ্রামের কারণে তারা অবস্থান পরিবর্তনে বাধ্য। আর এই আন্দোলন সংগঠনের প্রধান কৃতিত্ব ছিল দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের। সে-সময়ের সান্ধ্য দৈনিক ‘চাষী’ খবর দিয়েছিল এভাবে আওয়ামী লীগ রাজপথের আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। ৪ সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা অমান্য করে প্রাদেশিক রাজধানীতে ক্ষুধার্থ মানুষের মিছিল বের হয়। গুলিতে কয়েকজন হতাহত হয়। গুলিতে নিহত একজনের লাশ নিয়ে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিশাল মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।
প্রকৃতপক্ষে এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জনসমর্থনপুষ্ট ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নেতা হিসেবে বের হয়ে আসেন। রাজপথের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্র হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে প্রাদেশিক গভর্নর শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের পাঁচজন, কংগ্রেস থেকে দুজন, গণতন্ত্রী দল থেকে একজনসহ মোট ১১ জন নিয়ে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শেখ মুজিবুর নিযুক্ত হন শিল্প, বাণিজ্য, পল্লি উন্নয়ন ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী হিসেবে।
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব আন্দোলন হয়েছে, তার বিশ্লেষণ-মূল্যায়ন নানাভাবে হয়েছে। সে তুলনায় ১৯৫৬ সালে কীভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে এবং মাত্র বছর দুয়েক শাসনকালে কী কী গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সে আলোচনা কম। পাকিস্তানের একটি অংশে সরকার জনকল্যাণে কাজ করতে পারে, তার প্রমাণ মেলে। এ-সময়েই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল- দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দল ও মন্ত্রিসভার সদস্যপদ, দুটির মধ্যে দলের পদটিই বেছে নেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেছে- জেলা-মহকুমা-থানা পর্যায়ে তিনি বারবার ছুটে গেছেন। কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন, জনসমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন। দল ক্ষমতায় থাকার কারণে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তিনি কাজে লাগিয়েছেন দলের গণভিত্তি প্রসারের জন্য। এর সুফল মিলেছে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর। পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিকে গোলাম করে রাখার অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালের প্রবল ছাত্র-গণআন্দোলন সেটা নস্যাৎ করে দেয়। এ-সময়ের অভিজ্ঞতায় বঙ্গবন্ধু আরও একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন- পাকিস্তানের ‘অখণ্ডতা ও সংহতির আবেগ’ নিয়ে পড়ে থাকলে বাঙালির স্বাধিকারের স্বপ্ন পূরণ হবে না। এটাও বুঝে গিয়েছিলেন- কেবল রাজপথের মিছিল-সমাবেশ এবং হরতাল-ঘেরাও-অবরোধ নয়, সশস্ত্র সংগ্রামও সম্ভবত অনিবার্য। স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল করে তোলার জন্য কেবল রাজপথের জঙ্গি কর্মী যথেষ্ট নয়, বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিসেবী-পেশাজীবী- সকলের সক্রিয়তা চাই। প্রতিবেশী ভারতসহ আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন-সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি।
সংগঠন: সংগঠন গুছিয়ে তোলার প্রতিও ছিল সমান মনোযোগ। ষাটের দশকের প্রথম দিকের আন্দোলনে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল বাপক। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের ঐতিহাসিক হরতালে আদমজী-ডেমরা-তেজগাঁও-টঙ্গী অঞ্চলের শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এটা ছিল ষাটের দশকের শুরু থেকেই শ্রমিকদের সংগঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর সচেতন উদ্যোগের ফল। ঊনসত্তরের ২৪ জানুয়ারির গণ-অভ্যুত্থানও সংঘটিত হতে পেরেছিল শ্রমিকরা বিশাল বিশাল মিছিল নিয়ে ঢাকার রাজপথে চলে আসার কারণে। ছাত্র ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসার ও কর্মচারীদের সঙ্গে অভিন্ন কণ্ঠে তারা দাবি তোলে- আগরতলা মামলা তুলে নাও। শেখ মুজিবের মুক্তি চাই। পিন্ডি না ঢাকা ঢাকা ঢাকা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা স্লোগানের সঙ্গেও তারা একাত্ম অনুভব করে।
বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল নির্বাচন। ১৯৫৪ সালে এটা আমরা দেখেছি। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল ফাতেমা জিন্নাহকে সামনে রেখে। এ নির্বাচন উপলক্ষে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সভা-সমাবেশ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে তিনি ৬-দফা ইস্যুতে গণভোট হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জনসমর্থন সংগঠিত করার জন্য তিনি ছুটে গেছেন শহর-বন্দর-গ্রাম, বাংলার আনাচে-কানাচে। সামনে কঠিন লড়াই- এ বার্তা সে-সময়েই তিনি দিতে পেরেছেন এবং জনগণও তা উপলব্ধি করেছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঠিক তিন মাসের দিন ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’- এমন দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার প্রতি যে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন মেলে, তার প্রেক্ষাপট তো তৈরি হয়েই ছিল। তিনি সমবেত লাখ লাখ মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন আমার প্রতি আপনাদের আস্থা আছে? মুহূর্তে সমর্থনসূচক বার্তা মিলেছে। এই আস্থা গড়ে উঠেছে পাকিস্তানের ২৩ বছরে বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য তার নিরলস স্বপ্ন ও সাধনার জন্য এবং এ লক্ষ্য অর্জনে সময়োপযোগী কর্মসূচি ও কর্মকৌশল অনুসরণে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ থাকার কারণে। তিনি যে ‘বাংলাদেশ’ চাইছেন, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে। নিষ্ঠুর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এমন ঘোষণা ‘রাষ্ট্রদ্রোহিতা’, সেটা তার চেয়ে আর ভালো কেই-বা জানতেন। কিন্তু ততদিনে তো নিশ্চিত হয়ে গেছেন- বাঙালি স্বাধিকার চায়। কেউ তাকে দাবায়ে রাখতে পারবে না।
বাংলাদেশের জন্য অসহযোগঃ ১৯৭১ সালের ১ মার্চ যখন স্বাধীনতার চ‚ড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হলো, বিন্দুমাত্র দ্বিধায় পড়েননি জাতির পিতা। ৩ মার্চ নির্ধারিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে। বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, সেটা তিনি জানিয়ে দেন। বাংলাদেশ-এর সর্বত্র স্বাধীনতার সমর্থনে শুরু হয় মিছিল-সমাবেশ। প্রতিটি কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ। জনগণকে জাতির পিতা প্রস্তুত করেছিলেন বলেই একসঙ্গে গোটা দেশ প্রায় একসঙ্গে রাজপথে নেমে এসেছিল। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র-জনতার বিশাল সমাবেশে তোলা হয় স্বাধীনতার পতাকা, ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার এ পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েই শপথ গ্রহণ করে। ১ মার্চ দুপুর থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশই একমাত্র কার্যকরী নির্দেশ। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আয়োজিত বিশাল সমাবেশে তিনি বলেন, আমাদের আন্দোলন সত্যাগ্রহ, অসহযোগ। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চলবে।
১ মার্চ থেকেই সামরিক আইন বিধি ও নির্দেশ বাংলাদেশের মানুষ উপেক্ষা করে। ৭ মার্চ রেসকোর্সের সমাবেশ থেকে কার্যত স্বাধীনতা ঘোষণার আগেই আদালতের বিচারক, সরকারি ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর বেশিরভাগ বাঙালি সদস্য, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সংবাদপত্র-বেতার-টেলিভিশন কর্মী থেকে সর্বস্তরের জনতার যাবতীয় নির্দেশনা গ্রহণ করতে থাকে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িকে কেন্দ্র করে পরিচালিত ‘বিকল্প সরকারের কাছ থেকে’। বঙ্গবন্ধুর সরকারের আইনগত বৈধতা ছিল। কারণ জনগণ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে কেবল ‘বাংলাদেশ’ নয়, গোটা পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করেছিল।
৭ মার্চ রেসকোর্সের ঐতিহাসিক সমাবেশের পর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়। সামরিক সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার-টেলিভিশন-সংবাদপত্র সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ কেবল উপেক্ষা করেনি, একইসঙ্গে প্রচার করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর সরকার একদিকে ছিল আইনসম্মত এবং গোটা বাংলাদেশ ভূণ্ডের ওপর একইসঙ্গে তার কার্যকর কর্তৃত্ব নিয়েও কোনো সংশয় ছিল না।
অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই তিনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের প্রশাসনিক-অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করেন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসন- বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনার জন্য দায়িত্ব দেন পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ দলকে। ড. জিল্লুর রহমান খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রাম গ্রন্থে লিখেছেন, ‘৭ মার্চের পর মুজিব উদ্ভ‚ত বিভিন্ন সমস্যার নিরসনে সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্যই সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও করণীয় জারি করতে থাকেন। এর মধ্যে তার ৩ মার্চ ও ৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখের কর্মপন্থার পরিপূরক, ব্যাখ্যামূলক এবং যখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তখন নতুন নতুন নির্দেশনাও জারি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের পূর্ব অংশে কার্যত সরকার পরিচালনা করতে থাকে। মুজিবের এ সরকার হতে পারে অসাংবিধানিক, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তা বাংলাদেশের অধিকাংশ বাঙালির নিরঙ্কুশ সমর্থন ও স্বীকৃতির মাধ্যমে বৈধতা পেয়ে গেছে।’ [পৃষ্ঠা ১০৬]
মহাত্মা গান্ধীর ১৯২০ ও ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ ছিল সর্বাত্মক। জনসমর্থনের কোনো ঘাটতি ছিল না। ১৯৪২ সালের ব্রিটিশ শাসকরা ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন নিশ্চিত করেছিল- প্রায় ২০০ বছরের পরাধীনতার অবসান ঘটতে চলেছে। কিন্তু এ-সময়ে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম জনতার কাতারে শামিল হয়নি। বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম বাদে তারা মেনে চলে ব্রিটিশ শাসকদের হুকুম।
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ভণ্ডের কার্যকর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ে মনোযোগী হন- ‘প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’, এ নির্দেশকে বাস্তবে রূপদান। অসহযোগ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ রাখার বিষয়ে তিনি ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। একইসঙ্গে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে হলে সেটাই করা হবে, এ বিষয়েও কোনো সংশয় তার মনে ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রকাশ্যে সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করে। অস্ত্র হাতে রাজপথে মিছিল বের হয়। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রও সশস্ত্রযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। নারীরাও দলে দলে এতে এতে অংশ নেয়। সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্য, পুলিশ-ইপিআর-আনসার বাহিনীর বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার পাশাপাশি উৎসাহীদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশ জেগে ওঠে এক নতুন উন্মাদনায়- প্রয়োজনে রক্ত দেব, স্বাধীনতা আনবই।
অসহযোগ আন্দোলন কতটা স্বতঃস্ফ‚র্ত ও সর্বাত্মক ছিল, তার প্রমাণ মেলে এ ঘটনায়। বর্তমান রাজউক ভবনে (সে-সময়ের ডিআইটি ভবন) ছিল পাকিস্তান টেলিভিশন কার্যালয়। সেখানে ছিল কড়া সামরিক প্রহরা। কিন্তু বাঙালি কর্মীরা চলতে শুরু করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুসরণ করে। ২৩ মার্চ ‘পাকিস্তান দিবসে কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়বে না’- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এ নির্দেশনা আসার পর টেলিভিশনের বাঙালি কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেনÑ রাত সাড়ে ১০টার অনুষ্ঠান শেষে তারাও পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজাবেন না, চাঁদ-তারা খচিত পতাকা দেখাবেন না। পরিকল্পিতভাবে তারা অনুষ্ঠান দীর্ঘায়িত করেন রাত ১২টা পর্যন্ত। তারপর ঘোষণা করা হয়- ‘আজ ২৪ মার্চ…’।
অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন এবং ঢাকায় আসার আগ্রহের কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে স্বাগত জানাবেন কী-না, দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি যে উত্তর দেন তাতে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির যেমন পরিচয় মেলে, একইসঙ্গে কূটনীতির ভাষাও যে তিনি কতটা রপ্ত করে ফেলেছেন সেটা উপলব্ধি করতেও কারও সমস্যা হয় না। তিনি বলেছিলেন, ‘বাঙালিরা অতিথিপরায়ণ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অতিথি হিসেবে ঢাকা আসলে তাকে আমরা অতিথি হিসেবে অবশ্যই স্বাগত জানাব।’
আমরা জানি, এক দেশের রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান অন্য দেশ সফরে গেলে অতিথি হিসেবে গণ্য হন। ইয়াহিয়া খানকে বাঙালিরা অতিথি হিসেবে স্বাগত জানাবেÑ এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তায় আবিভর্‚ত হয়েছে।
তার এ ঘোষণা যে নিছক কথার কথা ছিল না, অসহযোগ আন্দোলন আরও সংগঠিতভাবে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে যে ৩৫-দফা নির্দেশনা জারি করা হয়, সেটা প্রকাশের তারিখ থেকেও স্পষ্ট। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার জন্য ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন ১৫ মার্চ এবং সেদিন থেকেই এটা কার্যকর করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বন্দর, আমদানি বাণিজ্য, রেলওয়ে, সড়ক পরিবহন, ডাক ও টেলিফোন বিভাগ, বেতার-টেলিভিশন-সংবাদপত্র, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি, কৃষি, সেচ, নির্মাণকাজ, সাহায্য-পুনর্বাসন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেতন, ট্রেজারি কার্যক্রম, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক, খাজনা ও কর আদায় না করা- সব কিছুই ছিল এর আওতায়। বলা যায়, ৩৫-দফা ছিল সার্বভৌম সরকারের নির্দেশনা। বাংলাদেশের সর্বত্র এটা মান্য করা হয়। একইসঙ্গে এটাও লক্ষ্য করি আমরা- অসহযোগ আন্দোলন চলছে। কিন্তু যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক। ৬ মার্চের পর আর হরতাল ডাকা হয়নি। মানুষের যেন দুর্ভোগ সৃষ্টি না হয়, সেটা ছিল মনোযোগের কেন্দ্রে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যেন থেমে না যায়, সে-বিষয়েও লক্ষ্য ছিল। শুল্ক-কর আদায় বন্ধ রাখায় নামি-দামি হোটেলে খাবারের দাম কমে যায়। পূর্বাণী ও হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালের খাবার সাধারণের আওতায় চলে আসে। অনেক পণ্যের মূল্য প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। উদ্ভ‚ত পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু তার অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত জানান- শুল্ক-কর আদায় চলবে, তবে তা জমা রাখা হবে বাঙালি মালিকানাধীন ব্যাংকে। জনগণ এটা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়।
বঙ্গবন্ধুর নির্দেশসমূহ মেনে চলায় জনগণের আগ্রহ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সাংগঠনিক দক্ষতা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার সরকার ক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রথম দিকের সাধারণ বিধি ও নিয়মের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ছাড় দেওয়া হতে থাকে এবং সেটাও সকলে বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগ এক ধরনের ব্যতিক্রমী সময়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সময়টি ছিল চরম প্রতিকূল। শক্র ছিল মেশিনগান-কামান-সঙ্গীন নিয়ে উদ্যত। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ডি জুড়ে সরকারকে একটি ডি ফ্যাক্টো সরকারে পরিণত করতে সক্ষম হন। স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন এ কারণেই অনন্য মাত্রা পেয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয় তারাও জাতির পিতার আন্দোলন পরিচালনার কৌশল যথাযথ অনুসরণ করে। এ সরকার সশস্ত্রযুদ্ধের জন্য স্বল্পতম সময়ে লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধাকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জিত করে রণাঙ্গনে প্রেরণ করে। ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় ১ কোটি শরণার্থীর থাকা-খাওয়া-চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয় দেখাশোনার জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে সর্বতো সহযোগিতা করে। মাত্র দুই মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত হয় পরিকল্পনা সেল, যারা মুক্ত স্বদেশের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে দেয়।
সুনিপুণ দক্ষতায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মধ্যেই এ সরকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক‚টনৈতিক অভিযান পরিচালনা করতে থাকে। তারা জাতিসংঘে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এর ফলে বিশ্বসমাজ পাকিস্তানি শাসকদের গণহত্যা অভিযানের নিন্দায় সোচ্চার হয় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবি জানায়। এসব পরিকল্পিত পদক্ষেপের কারণেই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করার চূড়ান্ত অভিযান শুরুর অনেক আগেই ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তা সর্বত্র নিন্দিত-ধিকৃত হতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র্র পারমাণবিক বোমা বহনকারী সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেও পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় রুখতে পারেনি। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য ও সহযোগী বাহিনীর প্রায় ৯৩ হাজার সদস্য রেসকোর্স ময়দানে মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। যে ময়দানে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন, সেখানেই হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারগার থেকে ব্রিটেন ও ভারত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে গ্রহণ করেন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব।